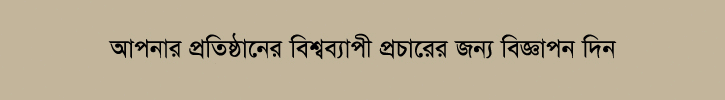আগামী জাতীয় নির্বাচনে ‘ভুয়া তথ্য ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা’ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, সামাজিক স্থিতি এবং নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ঝুঁকি তৈরি করছে—এমন সতর্কতা এসেছে এক সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনে।
গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশের অনলাইন তথ্যপরিবেশ এখন “অত্যন্ত ভঙ্গুর ও বিভক্ত”, যেখানে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতগতিতে এবং জনমত প্রভাবিত করার বিভিন্ন প্রয়াস দৃশ্যমান হচ্ছে।
ডিজিটাল অধিকার ও তথ্য বিশ্লেষণমূলক প্রতিষ্ঠান ‘ডিজিটালি রাইট’ পরিচালিত গবেষণাটি ‘ট্যাকলিং ইলেকশন ডিসইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ: বিল্ডিং কালেকটিভ রেসপন্সেস ফর ইলেক্টোরাল ইন্টেগ্রিটি’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় সম্পন্ন এই গবেষণা প্রতিবেদনটি রবিবার ঢাকার গুলশানে এক হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উন্মোচন করা হয়।
গবেষণার অর্থায়ন করেছে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও), তাদের ‘প্রমোটিং ইফেকটিভ, রেসপনসিভ অ্যান্ড ইনক্লুসিভ গভর্ন্যান্স ইন বাংলাদেশ’ কর্মসূচির আওতায়।
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, বিদেশি ও প্রবাসী প্রভাবকরা যেন এক ধরনের ‘ডিজিটাল প্রতিযোগিতায়’ নেমেছেন—যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর কনটেন্ট, প্রোপাগান্ডা নেটওয়ার্ক এবং বাণিজ্যিক কনটেন্ট নির্মাতারা সক্রিয়ভাবে জনমত প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।
গবেষণা বলছে, ভুয়া তথ্য এখন কেবল রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়—এটি জনআস্থা দুর্বল করা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি ও নারীর কণ্ঠরোধের শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। বিকৃত ছবি, মনগড়া ভিডিও এবং এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট নারী প্রার্থী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে, যা নির্বাচনের আগে ভয়ভীতি, হয়রানি ও ভোটার দমন বাড়াতে পারে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রস্তুতি এখনো ‘আশঙ্কাজনকভাবে দুর্বল’। প্রায় ১৭ কোটি মানুষের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ফ্যাক্ট-চেকারের সংখ্যা মাত্র ৪০ থেকে ৫০ জন। অধিকাংশ মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ফ্যাক্ট-চেকিং টিমই নেই। সাংবাদিক ও ফ্যাক্টচেকাররা প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাবে কাজ করছেন। নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ও নাগরিক সংগঠনগুলোর ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণও প্রায় নেই বললেই চলে।
এছাড়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো অন্য অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয় করছে না, আর নির্বাচন কমিশনেরও এই ডিজিটাল ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত নীতি, কাঠামো ও দক্ষতা নেই বলে গবেষণায় মন্তব্য করা হয়।
অনুষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন ডিজিটালি রাইটের গবেষণা প্রধান তিতির আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, “নির্বাচনকে সামনে রেখে খুব অল্প সময়ে বেশ কিছু বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে সংজ্ঞাগুলো অস্পষ্ট এবং অপব্যবহার রোধে কোনো সুরক্ষা কাঠামো রাখা হয়নি। এতে বোঝা যায়, অংশীজনদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি, ফলে আইনগুলোর যথেচ্ছ প্রয়োগের আশঙ্কা রয়েছে।”
তিনি আরও বলেন, “এই ধরনের বিধিমালা ব্যবহার করে বৈধ সমালোচনা ও ভিন্নমত দমন করা হচ্ছে—যেমনটি অতীতেও দেখা গেছে। মানবাধিকারের প্রভাব মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত না করে কোনো আইন বা বিধিমালা গ্রহণ করা উচিত নয়।”
আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, নির্বাচনি অপতথ্য মোকাবিলায় গণমাধ্যম, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এখন সময়ের দাবি।
প্রথম আলো অনলাইনের প্রধান শওকত হোসেন বলেন, “প্রচলিত গণমাধ্যমের তথ্য যাচাইয়ের পুরনো ধারা এখন আর যথেষ্ট নয়। এআই-নির্ভর বিভ্রান্তি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।”
ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, “ভুল তথ্য প্রতিরোধে ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। সরকারকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা সরকারকে এখন সেই অবস্থানে রাখেনি।”
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ‘আই’সোশ্যাল’-এর চেয়ারম্যান অনন্য রায়হান, এফসিডিও-এর গভর্নেন্স অ্যাডভাইজার এমা উইন্ড, দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, এবং ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী।